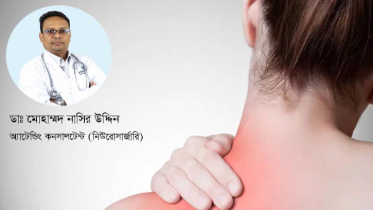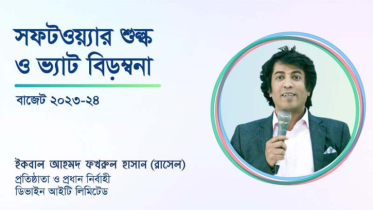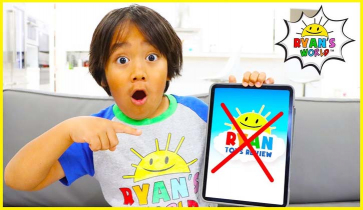ডিজিটাল যুগের যুদ্ধ এখন আর সীমান্তে হচ্ছে না, ঘটছে অনলাইন দুনিয়ায়। ব্যাংকের লেনদেন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সরকারি তথ্যভাণ্ডার থেকে নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা—সবকিছুই এখন সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে ব্যাংক হ্যাকিং, ডেটা লিক ও ফিশিং স্ক্যামের মতো ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গেছে উদ্বেগজনকভাবে। এই বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে—জাতীয় নিরাপত্তা এখন কেবল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রসারিত হয়েছে ভার্চুয়াল বিশ্বেও। প্রশ্ন হলো, এই নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত?
বাংলাদেশ ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রশাসন, ব্যাংকিং, শিক্ষা, বাণিজ্য—সব ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণে। কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ওয়েবসাইট, ব্যাংক, টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান, এমনকি সংবাদমাধ্যম পর্যন্ত সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। জাতীয় ডেটাবেইজে অনুপ্রবেশ, ভুয়া তথ্য প্রচার, র্যানসমওয়্যার আক্রমণ—এসব এখন এক বাস্তবতা।
বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি তিনটি স্তরে বিদ্যমান—রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হুমকি আসে প্রধানত বিদেশি হ্যাকার গ্রুপ ও রাষ্ট্র-সমর্থিত সাইবার অপারেশন থেকে। তারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে, বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালায়, কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে নাশকতা ঘটাতে পারে। ২০১৬ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা আমাদের জন্য এক চরম সতর্কবার্তা ছিল।
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঝুঁকি আরও জটিল। দেশের ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, টেলিকম, ই-কমার্স বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে ডেটা-নির্ভর হয়ে উঠছে। কিন্তু সুরক্ষার দিকটি সেভাবে শক্তিশালী হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানেই সাইবার নিরাপত্তা দল নেই, সঠিক এনক্রিপশন বা ফায়ারওয়াল ব্যবস্থা নেই, নিয়মিত নিরাপত্তা অডিটও হয় না।
ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিত্র আরও উদ্বেগজনক। সাধারণ নাগরিকের ডেটা ফাঁস, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণা, ডিজিটাল হয়রানি, কিংবা ফিশিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি—এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। একদিকে আমরা যত বেশি ডিজিটাল হচ্ছি, ততই আমাদের সাইবার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে।
জাতীয় নিরাপত্তায় সাইবার প্রতিরক্ষা কেন জরুরি-
অতীতে আমরা জাতীয় নিরাপত্তা বলতে বুঝতাম সীমান্তরক্ষা, সামরিক প্রস্তুতি বা গোয়েন্দা কার্যক্রম। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে সাইবার আক্রমণই হতে পারে এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশের ‘নীরব যুদ্ধ’। বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক কিংবা সরকারি তথ্যভান্ডার—সবকিছুই এখন সম্ভাব্য টার্গেট। একটি সফল সাইবার আক্রমণ গোটা দেশের অর্থনীতি ও প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিতে পারে। এ কারণে উন্নত দেশগুলো সাইবার নিরাপত্তাকে জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলের অংশ করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে Cyber Command, ভারতের রয়েছে National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), এমনকি প্রতিবেশী ভুটানও এখন নিজস্ব সাইবার সেনা গঠন করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সময় এসেছে একইভাবে চিন্তা করার। সাইবার নিরাপত্তা এখন কেবল আইটি বিশেষজ্ঞদের কাজ নয়; এটি আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।
কীভাবে মোকাবেলা করা যায়-
প্রথমত, একটি সমন্বিত জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি জরুরি। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা আলাদা আলাদা উদ্যোগ নিচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। একটি শক্তিশালী National Cyber Security Council গঠন করা দরকার, যেখানে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে কাজ করবে।
দ্বিতীয়ত, সাইবার সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ বাড়ানো প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মীদের নিয়মিত সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং দেয়া প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সাইবার নিরাপত্তা শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে স্থানীয় সাইবার বিশেষজ্ঞ তৈরি, হুমকি শনাক্তকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং সাইবার ফরেনসিক ল্যাব উন্নয়ন।
চতুর্থত, আইন ও নীতিমালা আধুনিকীকরণ জরুরি। সাইবার অপরাধ দমন আইন ও ডেটা সুরক্ষা আইনে যাতে নাগরিকের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষা পায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। নিরাপত্তার নামে যেন নজরদারির সংস্কৃতি না জন্ম নেয়।
পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সাইবার হুমকি সীমান্ত মানে না। তাই প্রতিবেশী দেশ, আঞ্চলিক সংস্থা ও বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সাইবার নিরাপত্তা উদ্যোগ ও এশিয়ান রিজিওনাল সাইবার ফোরামের সঙ্গে বাংলাদেশকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
অর্থনীতি ও সাইবার ঝুঁকি-
ডিজিটাল অর্থনীতির যুগে আর্থিক খাত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল পেমেন্ট, ই-কমার্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি—সবকিছুই সাইবার অপরাধীদের মূল লক্ষ্য। শুধু ব্যাংক নয়, স্টার্টআপ বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরও সচেতন হতে হবে। একবার ডেটা চুরি হলে তা পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সাইবার বীমা (Cyber Insurance) চালু করা যেতে পারে, যা ক্ষতি হলে আর্থিক সুরক্ষা দেবে।
বাংলাদেশ এখন স্মার্ট নেশন গঠনের পথে। আর এটি বাস্তবায়ন হবে তখনই, যখন স্মার্ট সিকিউরিটি নিশ্চিত হবে। প্রযুক্তি যেমন আমাদের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে, তেমনি এটি নতুন যুদ্ধক্ষেত্রও তৈরি করেছে। আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও ইন্টারনেট অব থিংস আমাদের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে অবস্থান করবে। তাই এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। সাইবার নিরাপত্তায় বিনিয়োগ মানে কেবল ডেটা রক্ষা নয়—এটি রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, জনগণের আস্থা ও অর্থনৈতিক টেকসই ভবিষ্যৎ গঠনের ভিত্তি।
বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে দাঁড়িয়ে। সামনে যতই আমরা প্রযুক্তিনির্ভর হব, ততই আমাদের নিরাপত্তার নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। তাই সময় এসেছে সাইবার নিরাপত্তাকে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের মূল স্তম্ভে স্থান দেওয়ার। সাইবার জগৎ এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ—কাজ, শিক্ষা, ব্যবসা, এমনকি প্রশাসন পর্যন্ত ছুঁয়ে গেছে এই ডিজিটাল বাস্তবতা। কিন্তু প্রযুক্তির এই বিস্ময় যেমন সম্ভাবনা এনেছে, তেমনি তৈরি করেছে নতুন ঝুঁকিও। একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় নিরাপত্তা মানে শুধু সীমান্তরক্ষা নয় তথ্য, অবকাঠামো ও নাগরিকের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
বাংলাদেশ যদি এখন থেকেই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলে, গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ায় এবং একটি শক্তিশালী সাইবার প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে পারে—তবে কেবল আক্রমণ ঠেকানো নয়, নিরাপদ ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ার নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হবে। আমাদের এখনই বুঝতে হবে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে তথ্যের, আর তার জয় নির্ভর করবে প্রস্তুতির ওপর। সময় এখন সচেতন হওয়ার এবং ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার।